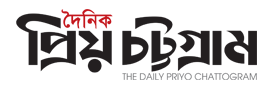মোহীত উল আলম
 আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে কবি নজরুল স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন ১৯৭২ সালের ২৪ মে। বঙ্গবন্ধুর বহু মৌলিক কাজের মধ্যে অন্যতম হলো কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেদিন কবির ছিল ৭৩তম জন্মবার্ষিকী। কিন্তু ১৯৪২ সাল থেকে জাগতিক চেতনা লুপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে তাঁর সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়া যথার্থ। নজরুল যেমন দু:খী মানুষের কষ্ট দেখে ফুঁসে উঠেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তেমনি দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। এই একই উদ্দেশ্যে যেহেতু দু’জনের জীবন ধাবিত ছিল, এটি প্রায় একটি ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা হয়ে পড়ে যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্রকে স্বাধীন করলেন, সেটারই জাতীয় কবি হবেন নজরুল। বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলা হয়, তেমনি নজরুলকে কবিতার রাজনীতিক বলা যায়। হাসপাতালে অসুস্থ কবি নজরুলের শয্যাপার্শ্বে উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু তাঁর (কবির) শিয়রে হাত রেখে সমবেদনা জানাচ্ছেন, এই সাদা-কালো ছবিটি তাই এই দুই মহাপুরুষের মেলবন্ধনের একটি অনুপম স্বাক্ষর।
আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে কবি নজরুল স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন ১৯৭২ সালের ২৪ মে। বঙ্গবন্ধুর বহু মৌলিক কাজের মধ্যে অন্যতম হলো কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেদিন কবির ছিল ৭৩তম জন্মবার্ষিকী। কিন্তু ১৯৪২ সাল থেকে জাগতিক চেতনা লুপ্ত ছিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে তাঁর সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়া যথার্থ। নজরুল যেমন দু:খী মানুষের কষ্ট দেখে ফুঁসে উঠেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তেমনি দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। এই একই উদ্দেশ্যে যেহেতু দু’জনের জীবন ধাবিত ছিল, এটি প্রায় একটি ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা হয়ে পড়ে যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্রকে স্বাধীন করলেন, সেটারই জাতীয় কবি হবেন নজরুল। বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলা হয়, তেমনি নজরুলকে কবিতার রাজনীতিক বলা যায়। হাসপাতালে অসুস্থ কবি নজরুলের শয্যাপার্শ্বে উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু তাঁর (কবির) শিয়রে হাত রেখে সমবেদনা জানাচ্ছেন, এই সাদা-কালো ছবিটি তাই এই দুই মহাপুরুষের মেলবন্ধনের একটি অনুপম স্বাক্ষর।
নজরুলের প্রথম পূর্ববঙ্গে আগমন, ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি। মতভেদ রয়েছে, এবং অনেক জীবনীকার বলছেন, তিনি ১৯১৩ সালের শেষের দিকে এসে পুরো একটি বছর ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে তারপর ১৯১৪ সালের শেষের দিকে চলে যান। এরপর তিনি রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ উচ্চ স্কুলে আড়াইটি বছর পড়ে নতুন গঠিত ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে নিবন্ধনকৃত হয়ে সৈনিক হিসেবে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করাচী চলে যান। ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন ক্রান্তিকালে পৌঁছেছে। মেসোপোটেমিয়ার কুত-অল আমরাতে বৃটিশরা দুই বছর আগে অট্টোমান তুর্কীদের কাছে বিরাট মার খেয়েছে। সে কুত-অল আমারা পুনরুদ্ধারের জন্য বৃটেন ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। সে কারণেই অতিরিক্ত রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে বাঙালী পল্টন গঠন ও রণক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কুত-অল আমারা পুনরুদ্ধার হয় (১৯১৭), এবং ১৯১৮ সালের শেষের দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯২০ সালের শুরুতে পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। করাচী থেকে নজরুল সে বছরের মার্চ মাসেই কলকাতা ফেরত আসেন, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে।
নজরুলের যুদ্ধে যাওয়া নিয়ে কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। অধ্যাপক প্রীতিকুমার মিত্র ধারণা করছেন যে নজরুলের শিয়ারশোল রাজ স্কুলের শিক্ষক ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত নিবারণ চন্দ্র ঘটক কর্র্তৃক তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষিত হতে। আবার ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি ‘সামরিক জাতি’ নয় বলে যে দুর্নাম ছিল সেটি ঘোচাতে। তাই তারা সদস্যদের অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ দিতেন। নজরুলের আধুনিক জীবনীকার গোলাম মুরশিদ উপরোক্ত যুক্তি খন্ডন করে বলছেন নজরুল যে আদৌ তাঁর শিক্ষক বা যুগান্তর গোষ্ঠী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের রণক্ষেত্রে ছুটে গেছিলেন তা মনে হয় না। তিনি বলছেন, তা হলেতো নজরুল দেশীয় সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতেন। কবি ওহীদুল আলম তাঁর “পৃথিবীর পথিক” গ্রন্থে নজরুল প্রসঙ্গে ১৯৩৩ সালে রাউজানে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্য সম্মেলনে নজরুল উপস্থিত ছিলেন বলে স্মরণ করেছেন। এবং বলছেন মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক নজির আহমদ চৌধুরী যখন অভিযোগ করেন যে নজরুল এবং মাহবুব-উল আলম যুদ্ধে যোগ দিয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করেছিলেন, তখন নজরুল প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, তাঁরা দারুণ তারুণ্যের বশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ‘কার বিরুদ্ধে কে জিতবে, কে হারবে, এসব তলিয়ে দেখার মন ও মেজাজ’ তাঁদের ছিল না।
আমি এ সঙ্গে আরেকটি কারণ যোজন করতে চাই। ১৯১৭ সালে নজরুলের বয়স ছিল আঠারো এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল সহ মিলে ১৬০ বছর চলছে তখন। অর্থাৎ আমরা ধরেই নিতে পারি যে ভারতবর্ষের আইন-আদালত থেকে শুরু করে দাপ্তরিক কার্যাবলী ও শিক্ষালয়ে যখন বৃটিশ পদ্ধতি ও মূল্যবোধ এবং তাদের সভ্যতার কপটতা সহ সকল কিছু ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে পড়ছিলো, তখন তাদের একটি শিক্ষা–‘জীবনের উদ্দেশ্য কী’ সেটিও নিশ্চয় ক্রমে বেড়ে ওঠা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজে স্তরীভূত হয়ে উঠছিল। মাহ্বুব-উল আলম তাঁর সরাসরি যুদ্ধের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গ্রন্থ “পল্টন জীবনের স্মৃতি”তে বলছেন, তিনি মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে কলেজ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে ফেললে, সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন। সেজন্য তিনি ভাবলেন যুদ্ধে যোগ দিয়ে সে খ্যাতিতে তিনি সহপাঠীদের ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। অর্থাৎ, একজন উঠতি বয়সের যুবকের নিজেকে পরিচিত করানোর জন্য তখন যুদ্ধে যোগদান করার আহ্বান ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম যুবাদের আকৃষ্ট করেছিলো। ইংরেজি সভ্যতার এই উচ্চাকাঙ্খা সংবলিত প্রতিযোগিতামূলক দিকটি এক দিকে যেমন মাহ্বুব-উল আলমের মতো যুবককে আকর্ষণ করেছিলো, তেমনি করেছিলো নজরুলকেও। কিন্তু নজরুল শেষ পর্যন্ত করাচী ছেড়ে মেসোপোটেমিয়ার রণক্ষেত্রে যাবার অনুমোদন পাননি, এবং প্রীতি কুমার মিত্র বলছেন এ নিয়ে তিনি একটু বিমর্ষও ছিলেন। কিন্তু গোলাম মুরশিদ অত্যন্ত সঠিক ধারণা করেছেন যে এটি শাপে বর হয়েছিলো, কারণ নজরুল আড়াইটি বছর এক নাগাড়ে সামরিক ছাউনির কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে নিজেকে কবি ও লেখক হিসেবে গড়ে তোলার অবিচ্ছিন্ন সময় পেয়েছিলেন।
কিন্তু যে কথাটি আমি বলতে চাইছি সেটি হলো, ইংরেজি সভ্যতার আদর্শের আঁতুড়ঘর যদি ইউরোপের রেনেসাঁকে ধরা হয়, তা হলে সে সময়কার ইংরেজ অভিজাত ঘরের যুবকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে জেন্টলম্যান বা অভিজাত যুবক হিসেবে গড়ে তোলা, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষের উঠতি উচ্চাকাঙক্ষী যুবকদের কেন ষ্পর্শ করবে না! যদি ইংরেজি ঘরানার আলোকে ইউরোপের রেনেসাঁর উদ্ভাবনীমূলক চিন্তাশক্তির প্রতিফলন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত পরিবারগুলোর সাহিত্য ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে দেখা যায়, তাহলে ইউরোপিয় রেনেসাঁ যুগের যুদ্ধপ্রীতিও কেন নজরুলের মতো যুবকদের সংক্রামিত করবে না! কারণ ইউরোপের রেনেসাঁর ভিত্তিমূল ছিল ব্যক্তিমানুষের উদ্বোধন–ব্যক্তিমানুষ সমাজের চেয়ে বড় এরকম একটি চিন্তা। রেনেসাঁ যুগের উপযোগিতামূলক রাজনীতির প্রবক্তা ম্যাকিয়াভেলি তাঁর “দ্য প্রিন্স” গ্রন্থে বললেন, একজন রাজশাসককে একাধারে যোদ্ধা ও জ্ঞানী হতে হবে। তাই ম্যাকিয়াভেলিসহ অন্যান্য দার্শনিকেরা মনে করতেন ‘যুদ্ধ’ মানব সমাজের জন্য একটি অবধারিত সত্য, এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই শান্তি আসবে। ধর্মীয়ভাবেও ‘জাস্ট ওয়ার’ বা ‘ন্যায়বাদী যুদ্ধে’র সমর্থন ছিল। কিন্তু রেনেসাঁ মনীষীদের আরেকটি ধারার–অত্যন্ত মানবতাবাদী ও শান্তিবাদী ধারার–নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস, যিনি তাঁর “কম্পলেইন্ট অব পিস” সহ বহু প্রবন্ধে বললেন যে যুদ্ধ কখনো শান্তি আনতে পারে না। একটি যুদ্ধ কেবল আরেকটি যুদ্ধের জন্ম দিতে পারে।
বৃটিশ শাসনের প্রভাবের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তির এ দ্বি-ধারার প্রবহমানতা লক্ষ করা যায়। এবং নজরুল কোন প্রবহমানতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন সেটি সহজেই অনুমেয়। তিনি যুদ্ধের রণদামামা বাজিয়ে কবিতা লিখলেন “কামাল পাশা”, “আনোয়ার পাশা” ও “বিদ্রোহী”। “বিদ্র্রোহী” কবিতার বিভিন্ন পংক্তি, যেমন “চির-উন্নত মম শির” , “আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ”, “আমি তাই করি ভাই যখন এ মন চাহে যা” ইত্যাদি পংক্তিগুলি অবশ্যই পরাধীন জাতির স্বাধীনতার আকুলতা থেকে সৃজিত এ কথা মানতেই হবে, কিন্তু সাথে সাথে যদি আমরা বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে রেনেসাঁ যুগের ইউরোপিয় রণদামামার কথা মনে রাখি তাহলে বুঝব নজরুল বস্তুত ম্যাকিয়াভেলির যুদ্ধজাত চিন্তাভাবনার আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন। এবং সে কারণেই “বিদ্রোহী” কবিতাটি অত্যন্ত যুদ্ধ-মুখরিত কাব্য হলেও তা’তে ব্যক্তিমানুষের চরম উদ্বোধন বৃটিশ শাসকদের পছন্দ হবার কথা। সে জন্য “বিদ্রোহী” কবিতাটি নিয়ে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বিচলিত ভাব আসেনি, এবং যে গ্রন্থে এ কবিতাটি নজরুল প্রকাশ করেছিলেন সে “অগ্নিবীণা” (১৯২২) কাব্যগন্থটিও ইংরেজ সরকার কখনো বাজেয়াপ্ত করেনি।
কিন্তু এর কিছু পরে ধূমকেতুর ১২তম বা অন্তিম সংখ্যায় প্রকাশিত “আনন্দময়ীর আগমনে” (১৯২২) কবিতাটি সত্যি সত্যি একটি এটম বোমা। আমার ধারণা, এটি বন্ধ করার পেছনে বৃটিশ সরকার হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের নেতৃগোষ্ঠীরও সমর্থন পেয়েছিলো। কারণ কবিতাটিতে আক্রমণের মিসাইল থেকে কাউকে বাদ দেয়া হয়নি। প্রথমেতো হিন্দুদের দেবি মা দুর্গাকে এক বিরাট খোঁচা দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করলেন তিনি: “আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?” তারপর, নজরুলের চিরকালের শত্রু মোল্লাদের প্রচারিত ধর্মীয় উন্মাদনায় আঘাত: “দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে, / নাইকো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্দী গড়ে। / ‘লানত’ গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে, / ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, ‘গলিজ’ মুঝে কোরান ভাঁজে।” (‘গলিজ মুঝের’ রূপক অর্থ নোংরা বা পচনশীল আত্মা।) এরপর গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে কটাক্ষ: “মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি, / খাঁড়ায় কেটে র্ক মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি!” নজরুলের চোখে অহিংস আন্দোলন ছিল “মাদী” ও “নপুংসকের” আন্দোলনস্বরূপ। তারপর অভিযোগ এবং আশা: “হঠাৎ কখন উঠলো ক্ষেপে বিদ্রোহিনী ঝান্সি-রানী, / ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলি নে তুই মা ভবানী। / এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতোকাল নিবি পূজা? / পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা!”
অন্যদিকে গান্ধীকে আমরা ইরাসমাসের ভাবধারায় শান্তিবাদী রাজনীতিক হিসেবে দেখতে পারি। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে নজরুল ১৯২১ সালে কংগ্রেসের পক্ষে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে “ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও” বলে গান করলেও, এবং গান্ধীর ওপর প্রশস্তিমূলক “উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন” শীর্ষক প্রবন্ধে “তাঁহার [গান্ধীর] আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহংকার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই ‘ছোটলোক’কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন” বললেও পরের বছর, অর্থাৎ ১৯২২ সালে “ধূমকেতু’র পথ” শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখলেন, “সর্বপ্রথম ‘ধূমকেতু’ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা . . . পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।” একটু আগেই বলেছি, “আনন্দময়ীর আগমনে”-র কবিতাটিতে তিনি অহিংস আন্দোলনকে “মাদী” এবং “নপুংসক” বলেছেন।
নজরুলের এই সুর গান্ধীর অহিংস আন্দোলন থেকে ঠিক ততটুকু দূরে যতটুকু দূরে ম্যাকিয়াভেলির ‘সঠিক যুদ্ধের’ ভাবনা ইরাসমাসের ‘শান্তিবাদী’ চিন্তা থেকে।
লেখাটা শুরু করেছিলাম নজরুল আর বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যুগলবন্দিতা নিয়ে। ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে নজরুলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মিল হচ্ছে সে জায়গায় যেখানে দু’জনেই মনে করেছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র পথ।
২.
বাংলাদেশের মাটিতে মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরশায়িত আছেন। আগেই বলেছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ কবিকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন ২৪ মে ১৯৭২ সালে। চারটি বছর নজরুল ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সেবাশুশ্রƒষার মধ্যে ছিলেন। ১৯৭৬ সালে এ মহাবিদ্রোহী কবির চোখ চিরতরে বন্ধ হয়। নজরুল তাঁর প্রথম দিকের “অভিশাপ” শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় লিখছেন, “যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে! / অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে– / বুঝবে সেদিন বুঝবে।” অভিমানের বিরাট একটা রেখা, যেটা প্রলম্বিত হয়ে তাঁর বিরহের গানগুলিতেও বেজে উঠেছে: যেমন, “আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভুলিতে,” বা আরেকটি গানে, “যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই কেন মনে রাখ তারে / ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে।”
ভুলেতো আমরা যাইনি, বরঞ্চ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কল্যাণে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছেন এবং আজকে বোধ করছি সবকিছু ছাড়িয়ে নজরুল ছিলেন বস্তুত মানুষের কবি। তাঁর “মানুষ” শীর্ষক কবিতাটি সর্বমানবতার জয়গান গাওয়া একটি ইশতেহার: “গাহি সাম্যের গান — / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!” ঠিক এর আগের লেখা “সাম্যবাদী” শীর্ষক কবিতার শুরু সে ঝড়-ঝঞ্ঝা তোলা চরণগুলি: “গাহি সাম্যের গান– / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান, / যেখানে মিশেছে হিন্দু–বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। / গাহি সাম্যের গান।”
ইতিহাসের কতগুলো রায় অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুলকে যদি আমরা একটি বৃক্ষ হিসেবে কল্পনা করি, সে বৃক্ষের শিকড় বাংলাদেশের মাটিতে প্রবিষ্ট থাকবে এটা যেন কালের গর্ভের কোথাও সৃজিত হয়ে গেছিল, এটি যেন বাংলাদেশ জন্মানোর আগে, এমনকি নজরুল জন্মানোর আগেই ঠিক হয়ে গেছিল। ইতিহাসের রাস্তাটিতে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ক্রমাগত ভ্রমণ করলে এরকম একটি আশ্চর্যজনক কিন্তু অনিবার্য সম্পর্কের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে।
জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির অন্যতম। একটি জনবহুল কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনের দেশে মানুষকে গিজগিজ করে বাঁচতে হয়, কিন্তু তারপরেও মানুষ যাতে মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারে তার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দু’টো প্রত্যয় নিশ্চিত করতে হয়। একটি হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার মুষ্টি থেকে বের হয়ে সমন্বয়বাদী চিন্তার প্রতিষ্ঠা করা, আরেকটি হচ্ছে ধনী-দরীদ্রের বৈষম্য দূরীভূত করে শোষণবিহীন অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এ দু’টোর সম্মিলিত সফলতা প্রকারান্তরে নিশ্চিত করে মানবতার প্রতিষ্ঠা। এ দুই ক্ষেত্রেই নজরুল আমাদের পথপ্রদর্শক। এটা বলা কঠিন, নজরুল সচেতনভাবে বেঁচে থাকলে তৎকালীন অনেক শীর্ষস্থানীয় বাঙালি মুসলমান কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিজ্ঞদের মতো পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দিতেন কি না, তবে মনে হয় দিতেন না–কারণ তাঁর সমগ্র রচনায় কোথাও সর্বভারতীয় চিন্তার বাইরে কিছু দেখা যায় না। নজরুলে দর্শনে ভারত ভাগ হোক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে এরকম ধারণার অনুপস্থিতি একবারেই নিশ্চিত–এবং অন্যদিকে তাঁর অচেতন হবার সময়–১৯৪২ সাল–থেকে দেশভাগ মাত্র পাঁচ বছরের মতো দূরে ছিল, কিন্তু তখনই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে এ কথা সঞ্চারিত হয়েছে যে মহাযুদ্ধটা শেষ হলেই ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশকে দু’টুকরো করে দিয়ে চলে যাবে। নজরুল সবসময় বিশ্বমানবতার মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, বিশেষ করে নির্যাতিত মানবতার মুক্তির ধ্যান ছিল তাঁর। সে পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তান বিভাজন তাঁর চোখে অনাবশ্যকরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল নিশ্চয়। সেজন্য এই সাম্প্রদায়িক তাড়নাকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেননি।
তবে যে কথাটি বলতে চাইছি, বাংলাদেশ যখন হয়েই গেল, আর নজরুল যখন হয়ে গেলেন এর জাতীয় কবি, নজরুল না জানলেও আমরা ইতিহাসের স্বাক্ষী হিসেবে বলতে পারছি, এর চেয়ে ভালো যুগলবন্দী আর হতে পারে না। অতীব জনবহুল দেশ বাংলাদেশ, আর অতীব অর্থনৈতিক অস্থিরতার দেশ বাংলাদেশ–সেখানে নজরুল কথিত অসাম্প্রদায়িক কিন্তু সমন্বয়বাদী মানবতা প্রতিষ্ঠা করা কত যে দুরূহ সেটি আমরা স্বাধীনতার পাঁচ দশকের কাছাকাছি এসেও খুব বাস্তবভাবে টের পাচ্ছি।
নজরুল এ দু’টো ক্ষেত্রেই–অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমতার প্রতিষ্ঠা–যে দু’টি প্রতিষ্ঠার পর নিশ্চিত হবে মানবতার জয়–বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মোক্ষম কথাটি হলো, ত্রাণপ্রক্রিয়ায় তিনিই আসলে আমাদের পথপদর্শক।
৩.
“মানুষ” কবিতায় নজরুলের “মানুষ এনেছে গ্রন্থ ; –গন্থ আনেনি মানুষ কোনো” পংক্তিটি তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের সারাৎসার। আমরা প্রায় সকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ভাষণে এবং রচনায় রবীন্দ্রনাথ-নজরুল এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আদর্শগত চিন্তার একটি ঐতিহাসিক-পরিব্রাজনশীল-ঐক্যের কথা বলি, সেটি আমরা রবীন্দ্রনাথ-বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে বলি এভাবে যে বাঙালি-সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের অপার্থিব প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং এ দু’টির আর্ন্তজাতিক উদ্বোধন হয়েছে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তিতে ও রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়াতে। আবার নজরুল-বঙ্গবন্ধুর সমীকরণের সময় এভাবে বলি যে নজরুল ধর্মের কুসংস্কার ও অর্থনীতির শোষণ প্রক্রিয়ার বলয় থেকে মুক্ত হয়ে নির্যাতিত মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটিই বঙ্গবন্ধু বাস্তবে রূপায়ন করেন।
ইতিহাসের একটি উল্লম্বন পাঠ আছে, আর একটি আনুভূমিক পাঠ আছে। ইতিহাসের ধর্মীয় পাঠ হচ্ছে উলম্বন পাঠ, যেখানে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটি মই আছে, যেখানে সবচেয়ে শীর্ষ ধাপে আছেন সৃষ্টিকর্তা, তারপর পার্থিব জগতের শাসকবর্গ, আর সবচেয়ে নীচে আছে প্রপীড়িত জনগন। অর্থাৎ, রাজা শাসিত সামাজিক কাঠামোর যে পরিচিতি আমরা পাই। সেদিক থেকে নজরুলের আক্রমণের শিকার ইতিহাস পাঠের এই রীতিটিই। “মানুষ” কবিতা থেকে আবার উদ্ধৃতি করা যাক: “কোথা চেঙ্গিস্্, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়? / ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার! / খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা? / সব দ্বার এর খোলা র’বে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা! / হায় রে ভজনালয়, / তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!” উল্লম্বন সামাজিক কাঠামোয় নানা ছুতায়, বিশেষ করে ধর্মীয় বাহানায়, শোষণ করার যে প্রক্রিয়াগুলো খোলা থাকে, তার নিরসন হয় আনুভূমিক গণতান্ত্রিক কাঠামোতে, যেটির প্রণোদনা নজরুলের কবিতায় আছে এভাবে: “তুমি শুয়ে র’বে তেতালার ’পরে, আমরা রহিব নিচে, / অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে!” (“কুলি-মজুর”)
নজরুলের দেহগত সক্ষমতা স্তব্ধ হয়ে যায় ১৯৪২ সালে, যখন বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে নবীন যুবক হিসেবে উত্থানরত। শহীদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে তখন তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনের ব্যাপারে সক্রিয়, যেটির উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচন সম্পন্ন করা।
পাকিস্তান হবার পরপরই আসলে নজরুলের সাম্যের গানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শোষণবিহীন বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্য এক হয়ে যায়। নজরুলের আনুভূমিক গণতন্ত্রের যে কাব্যিক দর্শন ছিল, সেটি বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতিয়তাবোধের উন্মীলনে খুঁজে পেলেন। “অসমাপ্ত আত্মজীবনী”-র ২৮৩ পৃষ্ঠায় ’৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়ের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু লিখছেন, “আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আপোস করবে না।” এ স্বায়ত্বশাসনের দাবি (৬ দফা) থেকে বাংলাদেশের সৃষ্টি। শুনেছি, বঙ্গবন্ধু কোন এক জনসভায় যখন শোষণবিহীন সমাজের কথা বলছিলেন তখন তাঁর পাশে দাঁড়ানো ভুঁড়িসর্বস্ব একজন নেতার প্রতি হাস্যরসিকতার ছলে বলেছিলেন যে তাঁর পেটটিও কাটা যাবে। অর্থাৎ ভুঁড়ির চিত্রকল্প দিয়ে বৈষম্যপূর্ণ অর্থনীতির কথা তিনি বললেন, আর বললেন, আনুভূমিক গণতন্ত্রের মধ্যে সবাই অর্থনৈতিকভাবে সমান থাকবে। এদিক থেকে নজরুল ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া যায়।
বাংলাদেশের নজরুল, নজরুলের বাংলাদেশ তাই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।
=শেষ=
২৪ মে ২০২২
পাদটীকা: লেখাটি মোহীত উল আলম গ্রন্থ “কবি নজরুল: বিদ্রোহীর এই রক্ত” থেকে নিয়ে কিছুটা পরিমার্জিত করে মোহীত উল আলম ফেসবুক ওয়াল নেয়া।