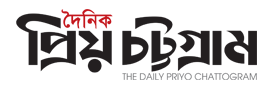আজ পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মজয়ন্তী। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।
স্বপ্নের ভিতরেই একটা কার্টুনের গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কালকে রাত্রে আম্মা আমারে ক্ষ্যাত বলছে। কারণ আমি বাসা সাজাতে চাইছিলাম কমলা রঙের কার্পেটের উপরে সবুজ রঙের সোফাসেট দিয়ে। শুধু তাই না, আমি চাই জানালায় ফুলওয়ালা পর্দা। জানালা খোলা থাকলে সেই পর্দা সিনেমার স্টাইলে উড়তে থাকবে আর বাইরের অন্ধকারে দাঁড়ালে ভিতরের রঙিন ঘর দেখা যাবে।
আম্মা নিরাশ করাতে দুঃখী মনে ঘুমাতে যাওয়ার ফলেই বোধহয় কার্টুনের গাড়িটা সবুজ ছিল আর রাস্তাটা কমলা। দুই পাশে অনেক রঙের ফুল আর ভিউকার্ডের প্রজাপতিগুলোর মতো বিশাল সব প্রজাপতি ধরফড় করতেছিল ফুলের উপরে। ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত বাজতেছিল দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে “ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো, আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো…এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়…”
গান শুনতে শুনতেই ঘুম ভাঙে। তারপরেও মনে মনে শুনছিলাম। এইরকম প্রায়ই হয় আমার, গান গাইতে গাইতে ঘুম থেকে উঠি। ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি কোনোদিন কিছু লিখেছিলাম কিনা। মনে হয় না। সেইদিন এক পত্রিকাওয়ালা বন্ধু লেখা চাইছিলেন উনাকে নিয়ে। উনার তো বলে আবার জন্মদিন। আমি সেই বন্ধুরে বললাম জন্মাইছেন ভালো কথা, এত ফেমাস কী করতে হইতে গেছিলেন উনি? প্রতি বছরই উনারে নিয়ে লেখা লাগে এত্ত লোকের। অপ্রকাশিত চিঠির স্টক তো এতদিনে মনে হয় শেষ, এখন ‘দেশ’ পত্রিকাওয়ালারা কী ছাপাবে আল্লাহ জানে। আমাদের মত দুধ-ভাত লেখকদের এই এক ব্যস্ততা হইছে, বড় বড় লেখকরা জন্মায়, নাইলে মারা যায় আর আমরা উনাদেরকে নিয়া লিখি। লিখলে তো লিখা যায় কতকিছুই!
ছোটবেলায় কোন একটা মেলায় যেন, বইমেলাও হইতে পারে, এক লোক টেবিলের উপরে অনেক সিরামিকের মূর্তি বেচতেছিল। তারমধ্যে একটা ছিল রবীন্দ্রনাথের, আলখাল্লা পরনে, দুই হাত পিছনে, লম্বা দাড়িওয়ালা মুখ সামনে একটু ঝুঁকে থাকা। আম্মা কিনলো একটা। রিকশায় আসতে আসতে জানতে চাইছিলাম এইটা কে এবং পাশেই সুন্দর সিরামিকের পাখিটা কেনার বদলে এই বুড়ার মূর্তিটাই কেন পছন্দ হইলো আম্মার! আম্মা বললো ইনার নাম রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি। ওইদিনই প্রথম নামটা শুনছিলাম কিনা জানি না, হয়তো আগেও শুনছি। তখন বোধহয় মাত্র স্কুলে ভর্তি হইছিলাম।
পরে ওই মূর্তিটা আমাদের বসার ঘরে শো-কেইসের মধ্যে থাকতো। সেইখানে আরো অনেক কিছুই ছিল। পাইরেক্সের ডিনার সেট, একটা ছোট্ট কফিকাপের সেট, করটিয়া সাদাত কলেজে তোলা প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর সাথে আব্বার ছবি, আব্বা তখন মাত্র প্রিন্সিপাল হয়ে গেছিলেন ওই কলেজে। ছবিটা ছিল সাদা-কালো। আমি ভাবতাম এই ইব্রাহীম খাঁ-ই বোধহয় ইব্রাহীম নবী। ছবিটার সামনেই মূর্তিটা ছিল – বিশ্বকবি। বিশ্ব মানে যে পৃথিবী তা ততদিনে জানতাম। ভাবতাম, ইনি তাইলে পৃথিবীর কবি। এইরকম নিশ্চয়ই আকাশ কবি, পানি কবিও আছেন।
রোববার ভোর। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল চলতেছে প্রবল পরাক্রমে। এই দেশে শীতের দিকে ঢলে পড়তে থাকা হেমন্ত। পাঁচটাও বাজে নাই। বাসার সবাই ঘুম। বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর খুব শীত। চাদর মুড়ি দিয়ে পোটলা হয়ে বসলাম লেখার চেয়ারে। এই যে বাড়ির বিভিন্ন ঘরে আমার ভালোবাসার মানুষগুলা আছে, ঘুমাইতেছে, তারা জেগে উঠবে কিছুক্ষণ পর, এই বোধটা কী শান্তির। আগে বহু কিছু চাইতাম, এখন এইটুকুই চাই। আমার ভালোবাসার মানুষেরা আমাকে ঘিরে থাকুক, তারা প্রতিদিন সকালে জাগুক, তাদের বেঁচে থাকার শব্দে আমার চারপাশ ভরে থাকুক…
টেবিলের পাশের জানালা দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটুকু দেখা যায় আর উল্টাদিকে অ্যান্ড্রুদের বাড়ি। রাস্তার আলোয় দেখতেছিলাম রাস্তার পিচ ভেজা বৃষ্টির পানিতে। গুনগুন করে গান বাজতেছিল মনের মধ্যে “ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী, এমনি…এমনি সেদিন উঠবে ভরি, চরবে গরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে…” একইসাথে একটা দীর্ঘশ্বাস আর আবহমানতার বোধ…এই যে আমি। কত ইম্পর্ট্যান্ট একজন মানুষ আমার কাছে, আমারে ঘিরে কত আয়োজন, কিছুই আসে যায় না…আমি থাকি আর না থাকি, এইভাবেই থাকতে থাকবে সবাই…”কাটবে দিন কাটবে, কাটবে গো দিন আজো যেমন দিন কাটে…”
এই গানটার কথা আমি প্রথম জানছিলাম মনো ভাইয়ের কাছে। সেদিনও কি শীতের রাত ছিল? রোজার দিন? একটা ভরন্ত সময়ের কথা সেটা। সেদিনই বোধহয় প্রথম আমি কনডেন্সড মিল্ক খাইছিলাম, অথবা, আমার স্মৃতিতে সেইটাই প্রথম হয়ে আছে। সেই মিল্কের টিন আনছিল মনো ভাই, বৃটিশ কাউন্সিলের পাশে ফুটপাতের উপরে তখন একটা মুদি দোকান ছিল, সেইখান থেকে। সেইটা যে আম্মা উনাকে আনতে বলছিল আমি জানতাম না।
মনো ভাই সন্ধ্যার সময় ম্যাজিশিয়ানের মতন বের করলো এই দুধের টিন, ওইটা আবার উপরে একটা বড়ো ফুটা আরেকটা ছোট ফুটা করতে হইলো। সেই টিন ব্রেড এর উপরে ধরলে ঘুরে ঘুরে জিলাপির প্যাঁচের মতন করে ঘন কনডেন্সড মিল্ক ঝরতেছিল। আর কী মিষ্টি একটা গন্ধ! অসম্ভব মজা লাগছিল খাইতে। তবে বাসার সবাই মিলে ছোট্ট একটা টিন, খুব বেশি কেউ পাই নাই। তখন থেকে আমার স্বপ্ন ছিল পুরা এক টিন কনডেন্সড মিল্ক খাইতে হবে। আমি এক টাকা এক টাকা করে জমাইতাম। আর মাঝেমাঝেই দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতাম তার দোকানে এখনও ওই অমৃতর মতন জিনিস সে রাখে কিনা! এরপর থেকে এখনো কনডেন্সড মিল্ক দেখলেই মনো ভাইয়ের কথা মনে আসে।
তো সেইদিন এইরকম সুখের সব ঘটনা ঘটার পরে রাতে মনো ভাই সিটিং রুমে বিছানা পেতে ঘুমাবে, তার আগে আমরা ছড়ায়ে ছিটায়ে গল্প করতেছি। উনি খুব সুন্দর ছবি আঁকতো। আর আম্মা উনারে বলছিল সুন্দর করে আব্বার নাম লিখে দিতে, দরজার বাইরে লাগানোর জন্য। মনো ভাই লম্বা একটা কাগজে লাল রঙে লিখলো “আলী আহমেদ রুশদী”। মনো ভাইয়ের লেখা ওই কাগজটাই আমাদের দরজার বাইরে লাগানো ছিলো আমরা অস্ট্রেলিয়া আসার আগে পর্যন্ত। সেইদিন একটা ছবিও আঁকছিল উনি…একটা মাঝি নৌকা বাইতেছে সন্ধ্যার সময়, সেই ছবির পাশে লেখা “আমি বাইবো না মোর খেয়া তরি এই ঘাটে, যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে…”।
আমি তখন পড়তে পারতাম তবে খুব ফ্লুয়েন্টলি না। কিছুটা হোঁচট খেতে খেতে পড়লাম লেখাটা, এইটা মানে কী বুঝলাম না। আম্মা আর মনোভাই মিলে আমারে অনেক কিছু বললো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ততদিনে জানি। তারপরে কতবার কতভাবে শুনলাম গানটা। তবু প্রতিবারই সেইরাতে আমাদের বসার ঘরটা মনে পড়ে। কেমন একটা শান্তি শান্তি ভাব ছিল সেদিন…তারপরেও কেন যেন মনে হইছিল এই সময়টা মনে রাখতে হবে, সবকিছু এমন থাকবে না। সেইটা কি এই গানের লাইনগুলোর আছর?
সেই ছড়াটাও শেখা হইছিল “তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে…”। তারপরে আশু ফুপু কিনে দিছিলো ‘সঞ্চয়িতা’। আমরা কয়েকদিনের জন্য ফুপুর কুমিল্লা শহরের বাসায় বেড়াতে গেছিলাম, তখন। ফুপু খুব প্রিয় লোক ছিলেন আমাদের। সারারাত গল্প করতাম উনার সাথে। উনি কুমিল্লায় নিজে নিজে একটা স্টিলের বিজনেস চালাতেন সেই আশির দশকের প্রথম দিকে। সঞ্চয়িতা কেনায় ফুপা রাগ হইছিলেন মুসলমানের বই না কিনে হিন্দুর বই কেনা হইছে বলে, তবে ফুপু সেই রাগে ডরান নাই।
দুপুর বেলায় ঘুম পাড়াতে নিয়ে আম্মা কবিতা শুনাতো সেই বই থেকে। “পুরাতন ভৃত্য” দুই লাইন করে পড়তো আম্মা তারপরে গল্পের মতো বলতো। আমরা আম্মার বলার ভঙ্গিতে হি হি হাসতাম, কেষ্টারে বন্ধুর মতন লাগতো, কবিতার শেষ হতে হতে আমরাও কানতে কানতে শেষ হইতাম। কেষ্টা, যে বাস্তবে কোথাও ছিলই না, সে মারা যাওয়াতে দুনিয়া কত খালি লাগতো আমাদের। বড় হওয়ার পরে অবশ্য যখন বেশ নতুন একটা প্রতিবাদী ভাব হইতো মনে, তখন ওই কবিতা তেমন ভালো লাগতো না। মনিবের জন্য মারা গেলেই চাকরের জীবন সার্থক এইরকম একটা ভাব লাগতো কবিতায়, বৈষম্যবাদী মনে হতো।
এখন এই পড়ন্ত বয়সে আবার ভালো লাগে কবিতাটা। এখন জানি দুনিয়ায় সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম বাদের বাইরেও বহু কিছু আছে, মওলানা রুমির সেই কবিতার মতোন “ঠিক এবং ভুলের নাগালের বাইরে একটা বাগান আছে, সেখানে তোমার সাথে আমি মিলবো”। কবিতাটা এখন আমি একটা পরম নির্ভরতার সম্পর্কের গল্প হিসাবে দেখি, একটা অলৌকিক ভালোবাসার বয়ান।
আরেকটা কবিতা আম্মা খুব পড়তো। ‘দুই বিঘা জমি’। এই কবিতা নিয়ে আব্বা-আম্মার ইতিহাস আছে। আব্বা যখন প্রথম আম্মাকে দেখতে গেল বড় মামার বাসায়, আম্মা তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। খাওয়া দাওয়ার পরে বড় মামা আম্মাকে বললো মেহমানদেরকে কবিতা পড়ে শুনাইতে। কিন্তু হাতে ধরায়ে দিল ক্লাস থ্রি না ফোরের একটা বাংলা বই। আব্বার ভাষ্যমতে সেই বই দেখে আম্মা রাগে ফেটে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলায়ে বললো “এইটা কী পড়মু!” তারপরে সঞ্চয়িতা টেনে নিয়া ‘দুই বিঘা জমি’ পড়তে শুরু করলো। আব্বা এখনো আম্মার নকল করে দেখায়, আম্মা নাকি সবাইরে চমকায়ে দিয়ে জোরসে বলছিল “ওটা দিতে হবে!” তো আম্মার সেই ডিমান্ড আব্বা কেমনে আর না রেখে পারে? তাই নিজেরেই দিয়ে দিল।
আমি ক্লাস-টু অথবা থ্রিতে পড়ার সময় আম্মা আমারে গান শিখাতে চাইলো। ছায়ানট তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে বসতো। সেইখানে ভর্তি করতে নিয়ে গেল মামা আমাকে। কিন্তু শেষমেষ ভর্তি হতে পারলাম নাচের ক্লাসে কারণ তখনও সরগম জানি না। মামা ছায়ানটের বারান্দায় দাঁড়ায়ে ছিল দুপুর বেলায়, আমি ঢুকছি নাচের ক্লাসে। তখন মামা শুনে একটা ক্লাসের মধ্যে একজন গাইতেছে “আমি মর্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কবো…”। সেই সুর শুনে সেইদিন একলা দুপুরে মামার কেমন লাগছিল আমি বুঝতে পারি।
সেদিনের সেই গানেওয়ালাই পরে আমার গানের স্যার হইছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় আসতেন আর আমি রবীন্দ্রসংগীত শিখতাম উনার কাছে। স্যারই প্রথম বলছিলেন গাইতে হলে উচ্চারণ ঠিক করা লাগবে। আমি রেওয়াজ না করলে বুঝতে পারতেন আর রাগ করে ভারি গলায় বলতেন “তুমি আজগে রেয়াজ করো নি!” উনি কোনোদিন “আজকে” বলতেন না। আমরা আড়ালে উনার “আজগে” নিয়ে হাসতাম, যদিও স্যাররে আমার খুবই ভাল্লাগতো।
তখন ভাবতাম রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বুড়া হইয়াই জন্মাইছিলেন। অথবা তাঁর জন্ম নিয়ে ভাবতাম-টাবতাম না। রবীন্দ্রনাথ মানেই ছিল শো-কেইসে রাখা সিরামিকের মূর্তিটা, দরবেশ দরবেশ ভাব। সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। পরে তো জানছিলাম উনিও ছোট ছিলেন, স্কুলে যাইতে না চাইলে উনারও পেট ব্যথা করতো। আরেকটু বড় হয়ে, মানে প্রেম প্রেম বয়স হওয়ার পরে, উনার যুবক বয়সের ছবি দেখে কত রকম কল্পনা করতাম! তারপরেও সেই বুড়া রবীন্দ্রনাথই চিরস্থায়ী হইলেন আমার মনে।
আব্বা আম্মার প্রিয় কবিতা “পুরষ্কার”। আম্মা এখনো মাঝে মাঝে হাসে আর বলে “রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে, এমনটি আর পড়িল না চোখে, আমার যেমন আছে…”। আমারে ভেঙ্গানোর জন্য আব্বা মাঝেমাঝেই বলে “ক্যামনে ব্যাটা পারিল সেটা জানতে!” ছোটবেলায় আমরা আব্বাকে ঘিরে বসতাম আর আব্বা আমাদেরকে কবিতা পড়ে শুনাইতো… ‘যেতে নাহি দিব’। আব্বা কানতো পড়তে পড়তে… “ওরে মোর মূঢ় মেয়ে, কোথা হতে কী শক্তি পেয়ে কহিলি এমন কথা… চরাচরে কাহারে রাখিবি ধরে, ছোট্ট দুটি হাতে, গরবীনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে? শুনি তোর শিশুমুখে স্নেহের প্রবল গর্ববাণী সকৌতুকে হাসিয়া সংসার টেনে লয়ে গেল মোরে, তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভরে, দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন, আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন…” আর আমি এই স্মৃতিচারণ করতে গিয়া ভাবতেছি আমরা একটা কান্দুরা ফ্যামিলি।
আব্বা অস্ট্রেলিয়া পিএইচডি করতে আসার সময় আমরা সবাই পিচ্চি পিচ্চি ছিলাম। ওই সময় ক্যাসেটে কবিতা রেকর্ড করছিলো আব্বা আমাদের জন্য, আর কিছু কথা। সেই রেকর্ড শুনতে শুনতে “শা-জাহান” মুখস্থ হয়ে গেছে। এখনো চাইলেই মনে মনে আব্বার অপ্রমিত উচ্চারণে শুনতে পাই “কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান, শুধু তব অন্তর বেদনা, চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল সেই সাধনা…”, প্রমিত উচ্চারণ না হওয়ার কারণে ভালো লাগা কমে না।
আব্বা অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পরে তার স্কলারশিপের জমানো টাকায় আমাদের প্রথম কার্পেট কেনা হইছিল। কার্পেট বিছায়ে আমরা বাসার পাঁচজন মিলা মিলাদ পড়ছিলাম। আবার সেই কার্পেটেই হারমোনিয়ম নিয়া বসে গাইছি “আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায়ও শুকায়ে মরি…”।
কয়েক বছর আগে আম্মা যখন হাসপাতালে ছিল, আমরা আম্মার বিছানার চারপাশে বসে ছিলাম। আব্বা দোয়া করলো, আমরা মোনাজাত করলাম আল্লাহর কাছে…বললাম, আম্মারে ভালো করে দিও আল্লাহ। ফেরার পথে বৃষ্টি হইছিল। গাড়ির কাচ ঝাপসা। মোহন সিং খাঙ্গুরা গাইতেছিলেন “বন্ধু রহো রহো সাথে…আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে…”। মনে হইতেছিল আম্মার জন্য আমার কান্নাগুলাই বৃষ্টি হইতেছে, গান হয়ে বাজতেছে।
ল্যাপটপ বন্ধ করে যতক্ষণে নিচে নামলাম, ততক্ষণে বৃষ্টি শেষে নরম ঝলমল করতে থাকা রোদ উঠছে। গিয়ে দেখি পায়ের কাছে হিটার ছেড়ে আম্মা বসে আছে। আমি গিয়ে তার গা ঘেঁষে বসলাম। আম্মাকে জড়ায়ে ধরে মাঝে মাঝে আবার তার ভিতরে ঢুকে যাইতে ইচ্ছা করে। নিজের আলাদা অস্তিত্ব নিয়া মাঝেমাঝে কী করবো বুঝতে পারি না… ব্যাকইয়ার্ডে জুঁইফুলের গাছটার পাতায় রঙ লাগছে। গাছটাকে দেখে মনে হইলো “এইজিং গ্রেসফুলি”… আর মনের মধ্যে গান বাজলো “রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে…”
কিছুদিন আগে হীরা মামারা আসছিলো। আমাদের আপন কিছু মানুষ মারা গেছেন গত এক বছরে। তাদের কথা হচ্ছিল, কত রকম স্মৃতি…মামাদেরকে বিদায় দেওয়ার সময় আব্বা আম্মা লাঠিতে ভর করে দরজা পর্যন্ত গেল। আমি আর সানিয়া ওদের পিছনে। আমি দেখলাম আব্বা আম্মার লাঠি একই তালে উঠতেছে নামতেছে।
ছোটবেলায় আমরা যখন ঢাকায় ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে থাকতাম, আব্বা একটা জমিদারী স্টাইলের লাঠি কিনছিলো শখ করে। ওইটা নিয়ে মর্নিং ওয়াকে যাইতো আর বলতো “বুড়া হইতেছি এখন তো লাঠি লাগবে” – সবাই হাসতো তখন, এখন কেউ হাসে না। মামারা গাড়িতে উঠতেছিল আর আম্মা লাঠি ভর করে দরজার সামনে দাঁড়ায়ে বলতেছিল – “সম্মুখ ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ, দেবো না দেবো না যেতে নাহি শোনে কেউ…”।
চাঁদ ছিল আকাশে, মেঘে ঢাকা, তবু তার আলোতে মেঘ সরতে দেখা যাচ্ছিল।